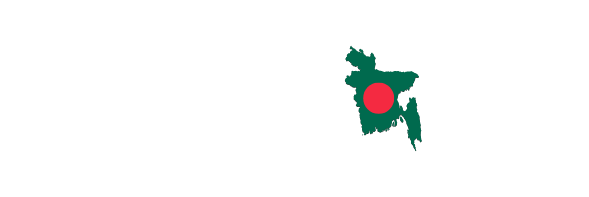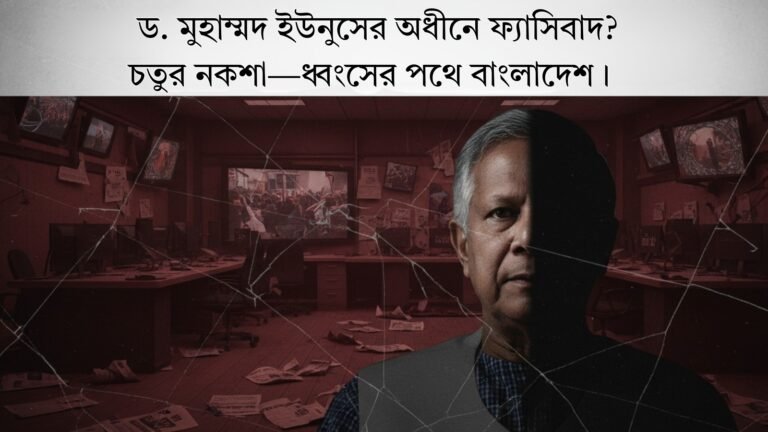✍️ ইঞ্জিনিয়ার শফিক ইসলাম (রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও আওয়ামী লীগের উপ-কমিটির সদস্য)
ভূমিকা
২০২৪ সালের জুলাই–আগস্টে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে ভূমিকম্প হলো, তা দেশের ইতিহাসে অন্যতম
অস্থির অধ্যায়। দীর্ঘদিনের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণআন্দোলন ও সহিংসতার প্রেক্ষাপটে পদত্যাগ
ও নির্বাসনে যেতে বাধ্য হলে নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি
অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। সামাজিক উদ্ভাবনের বিশ্বখ্যাত প্রবক্তা হিসেবে নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি
নিয়ে তিনি গণতান্ত্রিক সংস্কার, জাতীয় ঐক্য ও প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতার রোডম্যাপ তৈরির দায়িত্ব
পান।
কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই দেশি-বিদেশি বিতর্কে তাঁর প্রশাসন জড়িয়ে পড়ে। বিশেষত শেখ হাসিনার
আওয়ামী লীগ ও মিত্রগোষ্ঠীর অভিযোগ—ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার নব্য-ফ্যাসিবাদী
চর্চায় লিপ্ত: ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, মতদমন, বিচারব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও উগ্র/সাম্প্রদায়িক শক্তিকে
প্রশ্রয়। রাজনীতির বাইরে গিয়েও অভিযোগ ওঠে—অর্থনৈতিক অধঃপতন, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ক্ষয়,
ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের টার্গেটেড নিপীড়ন, ইতিহাস বিকৃতি, এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ
ভিত্তিকে “নিখুঁতভাবে ধ্বংস” করার প্রয়াস।
ইউনূসপন্থীদের পাল্টা যুক্তি—এ সবই ক্ষমতাচ্যুত এক শাসকের প্রপাগান্ডা; দীর্ঘ স্বৈরাচার-উত্তর
বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সামাল দিতে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।
এই দ্বিধাবিভক্ত বাস্তবতায় একই ঘটনাকে কেউ দেখছেন গণতান্ত্রিক সংস্কার, কেউ দেখছেন
কর্তৃত্ববাদে প্রত্যাবর্তন। নীচে মূল অভিযোগ, প্রেক্ষিত ও রাজনৈতিক প্রভাব সংক্ষেপে মূল্যায়ন করা
হলো।
নেতৃত্ব পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট
জুলাই ও আগস্টের শুরুতে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলনের পর ৫ আগস্ট ২০২৪ শেখ হাসিনা
পদত্যাগ করে ভারতে চলে যান। ক্ষমতাশূন্যতায় ৮ আগস্ট নাগরিকসমাজ, সামরিক বাহিনী ও আন্দোলনের
সমন্বয়কারীরা ড. ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ঘোষণা দেন—ঘোষিত
লক্ষ্য ছিল শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও অবাধ নির্বাচনের প্রস্তুতি।
নির্বাসন থেকে হাসিনার “ফ্যাসিস্ট শাসন” অভিযোগ
নির্বাসনে গিয়ে শেখ হাসিনা ইউনূস প্রশাসনকে “ফ্যাসিস্ট” আখ্যা দেন—সংসদ ভেঙে দেওয়া,
গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, বিরোধী দমন এবং সাম্প্রদায়িক-উগ্র গোষ্ঠীকে মদদ—এমন অভিযোগ তুলে
ধরেন।
বিরোধী রাজনীতির লক্ষ্যভিত্তিক দমন
বিশেষজ্ঞ ও অধিকারের সংগঠনগুলোর তথ্যে—আগস্ট–সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ পুলিশ ৯২,০০০-এর বেশি
লোকের বিরুদ্ধে হত্যা ও অশান্তি-সংশ্লিষ্ট মামলার নথি করে; অনেক মামলায় নাম-পরিচয়হীন অসংখ্য
আসামি। আলোচিত আওয়ামী লীগ নেতাদের একাধিক মামলায় গ্রেপ্তার, বিচারপ্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক
প্রতিশোধের হাতিয়ার বানানোর অভিযোগ—সব মিলিয়ে বিরোধীদের মধ্যে ভয়ব্যাপী পরিবেশ তৈরি হয়।
সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ বাড়ে
শেখ হাসিনা বিদায়ের পরপরই হিন্দু–খ্রিস্টান–বৌদ্ধসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে ব্যাপক
সহিংসতা, অগ্নিসংযোগ, মন্দির ভাঙচুর, দখলদারি ও হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ ওঠে। উদাহরণস্বরূপ,
প্রথম আলো জানায়—সরকার বদলের পর ১৫ দিনে ৪৯ জেলায় ১,০৬৮টি ঘটনা। সংখ্যালঘু ঐক্য পরিষদ
এক সপ্তাহে ৫২ জেলায় ২০৫টি হামলার নথি দেয়। সরকার অন্তত ৮৮টি মামলা ও ৭০+ গ্রেপ্তারের কথা
জানালেও অ্যামনেস্টি/এইচআরডব্লিউ–এর সমালোচনা—সংরক্ষণ ও ন্যায়বিচারে ব্যর্থতা; বহু হিন্দুর
ভারতে পালানোর ঘটনাও আলোচ্য হয়।
সরকারের অস্বীকার ও “ডাউনপ্লে”
সরকার সহিংসতা নিন্দা করলেও বহু সংখ্যার হিসাবকে “অতিরঞ্জিত/রাজনৈতিক” বলে কমিয়ে দেখায়।
কিন্তু সংখ্যালঘু নেতৃত্ব, নাগরিকসমাজ ও আন্তর্জাতিক মহল এসব ব্যাখ্যায় সংশয়ী; নিরপেক্ষ তদন্ত
ও বাস্তব ক্ষতিপূরণের দাবি জোরালো হয়।
গণমাধ্যমে দমন-পীড়ন
আগস্ট ২০২৪–মার্চ ২০২৫-এ Rights & Risks Analysis Group জানায়—৬৪০ সাংবাদিক
মামলা/সহিংসতা/স্বীকৃতি বাতিল/আর্থিক তদন্তে টার্গেট হন। অনেকে অ্যাক্রেডিটেশন হারান,
সম্পাদকদের হটানো হয়, মালিকানা/নেতৃত্বে শাসকপন্থী রদবদল, বিএফআইইউয়ের আর্থিক
নজরদারি—সব মিলিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ (self-censorship) বাড়ে।
মতদমনমূলক আইন–কানুনের ব্যবহার
সাংবাদিক–বিরোধী–সিভিল সমাজ নেতাদের বিরুদ্ধে পুরনো ও বিস্তৃত আইন ব্যবহার করে কমপক্ষে
১১৩টি ফৌজদারি অভিযোগ; গ্রেপ্তার–হেফাজতে নির্যাতন–নির্বিচার আটক—বিচারবিভাগের
রাজনৈতিককরণের অভিযোগ জোরালো।
“মিডিয়া রিফর্ম কমিশন” ও “ফ্যাক্টস ইউনিট”
ভুয়া খবর ঠেকানোর শ্লোগানে নতুন কাঠামো গড়ে তোলা হলেও সাংবাদিকরা এগুলোকে সেন্সরশিপ ও
নজরদারির টুল হিসেবে দেখছেন।
আন্তর্জাতিক উদ্বেগ ও মানবাধিকার
এইচআরডব্লিউ, অ্যামনেস্টি, ভারতের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র—বহু পক্ষ সংখ্যালঘু সুরক্ষা, মতপ্রকাশের
স্বাধীনতা ও যথাযথ প্রক্রিয়ায় গুরুতর ঘাটতি দেখছে। রাষ্ট্রপৃষ্ঠপোষক ভয়ভীতি–বহির্বিচার—এসব
অভিযোগে সংস্কারের প্রতিশ্রুতিতে আস্থা ক্ষীণ।
ইউনূসপন্থীদের প্রতিরক্ষা
ইউনূসের সমর্থকেরা বলছেন—সবই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ধারাবাহিকতা; নোবেলজয়ীর বৈশ্বিক মর্যাদা
থাকায় তাঁকে হেয় করতে এসব মামলা–মোকদ্দমা। শ্রম আইনভিত্তিক রায় বাতিলসহ কিছু মামলায়
আদালতের রিলিফ পাওয়াকে তাঁরা ‘হয়রানির প্রমাণ’ হিসেবে ধরছেন; সমালোচকেরা আবার এটিকে
বিচারব্যবস্থায় প্রভাব বলেই আখ্যা দেন।
সিভিল সার্ভিস ও মিডিয়ায় রদবদল
শীর্ষ আমলা–মিডিয়া–প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক বদলি ও অপসারণের অভিযোগ—বিএনপি/জামায়াতঘেঁষা
নিয়োগ–পদায়নের অভিযোগে মেরুকরণ তীব্র হয়; চাকরিক্ষেত্রে অনিরাপত্তা বাড়ে।
আত্মনিয়ন্ত্রণের (Self-Censorship) বিস্তার
২০২৪–২০২৫ সময়ে সাংবাদিক হয়রানি/সার্টিফিকেট বাতিল/আর্থিক তদন্ত ২৩০% বেড়েছে—বলার মতো
পরিসংখ্যান হাজির হচ্ছে। ফল: অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হিমশিম, বিরোধীদর্শী কণ্ঠ স্তব্ধ।
মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা–রাজনীতির কেন্দ্রে
জামুকা আইনে “জাতির পিতা” উল্লেখ কমানো ইত্যাদি ইস্যুতে ইতিহাস–পরিচয়–ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে
নতুন মেরুকরণ। সরকার বলে “অরাজনৈতিক নিরপেক্ষতা”, সমালোচকেরা দেখেন “মুক্তিযুদ্ধ-বিদ্বেষী
ন্যারেটিভ” জোরদার।
সিভিল সোসাইটিকে আতঙ্কিত করা
মানবাধিকারকর্মী–সংখ্যালঘু নেতা–বিরোধীদের বিরুদ্ধে নির্বিচার আটক, মামলার জাল, পুলিশি সুরক্ষা না
দেওয়া—এমন রিপোর্ট ঘন ঘন। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো নাগরিক পরিসর সংকোচন নিয়ে সতর্ক করছে।
নির্বাচন ও সংস্কারের প্রতিশ্রুতি
তীব্র সমালোচনার মধ্যেও ইউনূস ঘোষণা দেন—ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ জাতীয় নির্বাচন, হালনাগাদ ভোটার
তালিকা, সব দলের অংশগ্রহণের সুযোগ ইত্যাদি। কিন্তু বিরোধী দমন, গ্রেপ্তার, আ.লীগের ওপর
বিধিনিষেধ—সব মিলিয়ে সন্দেহ কাটছে না।
প্রেস–স্বাধীনতার পরিমিত চিত্র
আগস্ট ২০২৪–জুলাই ২০২৫-এ ৮৭৮ সাংবাদিক নানামুখী টার্গেটে—গত বছরের তুলনায় ২৩০% বেশি; নতুন
ফৌজদারি মামলায় ৫৫৮% বৃদ্ধি—সাংবাদিকতায় “শীতল সন্ত্রাস” স্পষ্ট।
দমননীতি “ন্যায়সঙ্গত” করার যুক্তি
সরকার বলছে—জুলাই–আগস্ট ২০২৪–এর “অসাধারণ সহিংসতা”র প্রেক্ষিতে কঠোর নিরাপত্তা/আইনি
ব্যবস্থা জরুরি, পূর্বতন শাসনের “মানবতাবিরোধী অপরাধ”ের বিচার শুরু হয়েছে। সমালোচকদের
মতে—বর্তমান দমন কৌশল ন্যায়বিচারের বাইরে গিয়ে বর্তমান বিরোধীকেই দমন করছে।
গভীরতর মেরুকরণ
এক পক্ষের কাছে “দ্বিতীয় মুক্তি”, আরেক পক্ষের কাছে “নতুন স্বৈরাচার”—এই দুই ন্যারেটিভে সমাজ
বিদীর্ণ। আ.লীগের ওপর আইনি বিধিনিষেধ, বিএনপি–ইসলামপন্থীদের প্রতি কথিত পক্ষপাত,
ধর্মনিরপেক্ষ কণ্ঠকে প্রান্তে ঠেলে দেওয়া—সব মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানগত নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন বাড়ছে।
উপসংহার: নোবেলজয়ীর শাসনে “নিখুঁত ধ্বংস” ন্যারেটিভের হিসাব-
নিকাশ
ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে নব্য-ফ্যাসিবাদের অভিযোগ—ঐতিহাসিক অস্থিরতা, তীব্র মেরুকরণ ও পারস্পরিক
বিধ্বংসী রাজনৈতিক কৌশলের প্রেক্ষিতে বিচার্য। শেখ হাসিনার পতনকে যে জনগণ “শাসনমুক্তি”
ভেবেছিল, তারা এখন দেখছে—ঘুরেফিরে একই কর্তৃত্ববাদী ধাঁচের পুনরাবৃত্তি।
“নিখুঁত ধ্বংস” থিসিসের যুক্তি
অর্থনীতি: প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগে ধস, শিল্পোৎপাদন ও ব্যাংকিংয়ে সংকট,
মুদ্রাস্ফীতি–বেকারত্বে সরকারি ব্যর্থতা।
সমাজ: সংখ্যালঘু–শিক্ষক–কর্মী–শাসকদল–সমর্থকদের ওপর সহিংসতা ও উগ্রতায় ভীতিকর
পরিবেশ; শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্কট, তরুণদের র্যাডিকালাইজেশনের শঙ্কা।
রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব: জাতীয় সম্পদ নিয়ে অস্বচ্ছ সমঝোতা—প্রাতিষ্ঠানিক ভাঙন ও
কর্তৃত্বহানি।
ইউনূসের প্রতিরক্ষা
ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার: প্রাতিষ্ঠানিক পচন পুরোনো শাসন থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে
প্রাপ্ত—ফলে ‘শক থেরাপি’সদৃশ সংস্কার অনিবার্য।
অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট ঐক্য: সব পক্ষকে এক মঞ্চে আনার চেষ্টা; সত্য
উদ্ঘাটন–সংস্কার–নির্বাচন—তিন স্তম্ভে রূপান্তর।
বিচার ও পুনর্গঠন: অতীত নৃশংসতার বিচারে ট্রাইব্যুনাল, ১৯টি কাঠামোগত সংস্কারের
রোডম্যাপ, প্রশাসনিক স্বচ্ছতার উদ্যোগ।
মূল্যায়নের সীমা
কে কোন ন্যারেটিভ মানবেন—তা রাজনৈতিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল। স্বাধীন পর্যবেক্ষকেরা
বলছেন—দমন–বর্জন–পতন—দুই শাসনেই পারস্পরিক অভিযোগ হিসেবে বিদ্যমান; উভয়েই “নব্য-
ফ্যাসিবাদ” তকমা দিয়ে বৈধতা জেতার চেষ্টা করছে।
চূড়ান্ত কথা:
ইউনূস-পর্ব বাংলাদেশের বাস্তবতা দেখায়—অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা বদল, পারস্পরিক বৈধতাহরণ,
প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষয় ও সামাজিক ফাটল কেবল গভীরতর সংকট ডেকে আনে।
অর্থনীতি–গণমাধ্যম–রাজনীতির ক্ষতি বাস্তব; তবে সবকিছুর দায় এক ব্যক্তির উপর চাপানোও
সরলীকরণ। ভবিষ্যতের যে কোনো সরকারের জন্যও জরুরি—গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার ও আইনের শাসনে
কার্যকর সুরক্ষা-কবচ গড়ে তোলা—যাতে পুনরায় কর্তৃত্ববাদ, দায়মুক্তি ও বিভেদের চক্রে দেশ না পড়ে।